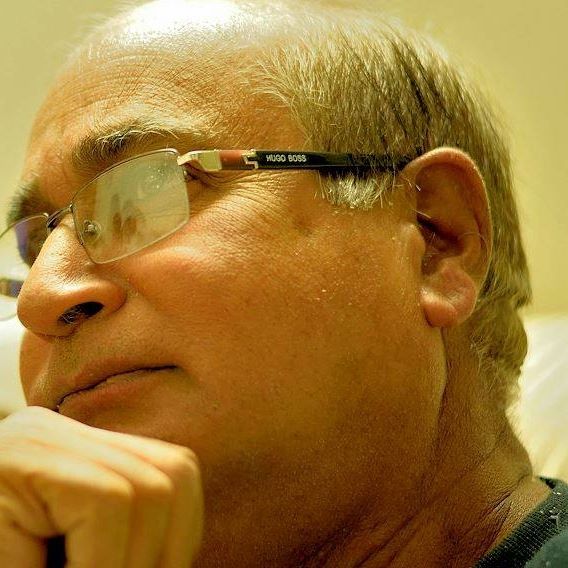(Born: May 7, 1861, Kolkata
Died: August 7, 1941, Jorasanko Thakurbari, Kolkata, India)
পলাশী যুদ্ধের সতের বছর পর বাংলার এক ক্রান্তিকালে লালনের জন্ম ১৭৭৪ (মতান্তরে)। এর মাত্র নয় বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছে।
লালনের দীর্ঘ জীবন ব্রিটিশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে স্পর্শ করেছে। এই সময়কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, বাবু সংস্কৃতির জনক ও পৃষ্ঠপোষক নতুন সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছে- ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি সংগ্রাম উপমহাদেশ দেখেছে।
এই সময়ের মধ্যে হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা হিন্দু কলেজ, বেথুন কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে বাঙালির সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা কর্মকাণ্ডে বাঙালির জীবন স্পন্দিত। তবে মূল বিষয় হলো বাঙালির এই প্রাণস্পন্দন শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক এবং তা এই মহানগরীর ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সুফল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়তে ঢের সময় লেগেছিল।
শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড থেকে অনেক দূরে ছিলেন লালন।
বাউলতত্ত্বের পটভূমিকাঃ
কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণ সার্বজনীন মানবচেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে বাঙালি মুলসলমানদের রক্ষণশীল মনোভাব, আরেকদিকে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চিন্তার পরিপোষক বাঙালি হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য এই নবজাগৃতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়েছিল। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ (Renaissance)
হিন্দু-মুসলমান মিলিত প্রয়াসের ফসল নয়, বরং তা উভয়ের মধ্যেকার ভেদনীতি ও বিদ্বেষকে ত্বরান্বিত করেছিলো।
সকল কালেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গণ্ডীর বাইরে মানবমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তারা সমন্বয় ও মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন। এমনই একজন হলেন লালন শাহ। মানুষকে সকল কিছুর উপরে স্থান দিয়ে তাঁর দর্শন গঠন ও প্রচার করেছেন তিনি। লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ, তাঁর উপর তিনি সাধনকর্মে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল। শিক্ষিত বাঙালির নবজাগৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের খবর জানা বা এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ও প্রয়োজন কোনোটাই তাঁর ছিলো না বললেই চলে। তবুও গ্রামীণ জীবনে নিজ সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে যে তরঙ্গ তিনি তুলেছিলেন, তা’ বিস্ময়কর ও অসাধারণ।
বাউলমতের প্রবর্তনের পেছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, অবিচার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিলো। সামাজিকভাবে বৈষম্যগ্রস্ত ও ধর্মীয় আচার বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার ধর্মমত বা দর্শনের সন্ধান অতি স্বাভাবিক ছিল। লালনের জীবনের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এক তীর্থযাত্রায় লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীরা পথিমধ্যেই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। তখন এক মুসলমান পরিবার তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে সে যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু বাড়ি তার আর ফেরা হয়নি। মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করার কারণে নিজ গৃহে, এবং হিন্দু সমাজে তাঁর আর জায়গা হয়নি। স্বজন বিচ্ছিন্ন, ভগ্নহৃদয় লালন শেষে সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে এসে বাউলমতে দীক্ষা নেন।
লালনের মানবধর্মঃ
লালনের গানে ধর্ম সমন্বয়, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সাথে তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণের কোনো অমিল পাওয়া যায়নি।
ফোঁটা, তিলক, টিকি-টুপি নিয়ে ধর্মের বাহ্যিক যে আচার, তার প্রতি লালনের কোনো আগ্রহই ছিলো না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন-
“মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সব দেবা-দেবী
ভোলে না সে এসব রূপি
ও যে মানুষ রতন চেনে।।”
প্রাণহীন অসার বস্তু, অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির তুলনায় মানবীয় কর্ম ও মহিমাকে বড় করে দেখিয়েছেন লালন। তাঁর এই মানব মহিমা কীর্তন সেই যুগে দুর্লভ ছিল। নিচের এই গানটিতে লালন মানববন্দনার যে সুর তুলেছেন তার তুলনা গ্রাম্য সাহিত্যে তো নেই-ই, ভদ্র সাহিত্যেও বিরল-
“অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি- মানবের উত্তম কিছুই নাই।
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভারা না ডোবে।।”
শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার বিরুদ্ধে লালন সবসময়ই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ভেদনীতির বিরুদ্ধে সদর্পে তিনি বলেছেন-
“জাত না গেলে পাই না হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে?
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।।” – কি অসাধারণ তাঁর এই বাণী।
রবীন্দ্রনাথের উপর লালনের প্রভাব
বাউল দর্শন ও সঙ্গীত বাংলার অনেক কৃতী মানুষদেরই আকৃষ্ট করেছে। তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শনের উঠোনে বিচরণই করেননি শুধু, তিনি এর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। বাউল সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতায় বাউলের প্রসঙ্গ ও বাউল দর্শন নানাভাবে এসেছে। যেমন তার ‘অভিসার’ কবিতাটির কথাই ধরা যায়।
“আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!”- প্রাণের গভীরে গিয়ে আঘাত করে সে কবিতার মর্মবাণী। আবার তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতাতেও বাউলচেতনার সাথে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে-
লালনের ‘মনের মানুষ’কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খুঁজেছেন তাঁর নিজের মনোভূবনে। ক্রমশঃ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন ‘রবীন্দ্রবাউলে’। বাউল গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বাউলের বেশভূষায়। বাউলের আলখাল্লা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রমানসে বাউল প্রভাবের মূলে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত লালনচর্চা ও লালন শিষ্য সম্প্রদায়ের সাহচর্য।রবীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছিলেন রবীন্দ্র বাউলে।
জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহ এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। তিনি লিখেছেন-
“কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।”
রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র-১৩১৪ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর “গোরা” উপন্যাসে-
আলখাল্লা পরা এক বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল:
“খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।”
একই গানের উদ্ধৃতি মেলে রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’ অধ্যায়ে। উপরের দু’টি পঙক্তিই উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন-
“দেখিলাম, বাউলের গানেও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!”
১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে ‘The Philosophy of Our People’ শীর্ষক ভাষণে লালনের ‘অচিন পাখি’ গানটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লালন ও বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক (Percy Bysshe Shelley) “শেলীর” মধ্যে তুলনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন-
“…only Shelley’s utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by the mystic transcendentalism.”
“এমন মানব জনম আর কি হবে
ও মন যা কর তা ত্বরায় কর এই ভবে।”
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ‘ছন্দের প্রকৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লালনের উক্ত পঙ্কতিমালা উল্লেখ করে এর সমালোচনায় বলেন-
“এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটবড় নানা ভাগে এঁকেবেঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।”
লালনের সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। নিশ্চিত কোনো খবর বা তথ্য এ বিষয়ে পাওয়া যায় না। তবে লালনের শিষ্যদের অনেকের সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে, সে বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে।
শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। জানা যায়, ছেউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৯৮টি গান কপি করিয়ে নেন। এই খাতা সম্পর্কে সনৎকুমার মিত্র বলেছেন-
“…রবীন্দ্র ভবনের খাতা দুটিই ছেউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং যেভাবেই হোক তা রবিবাবুর হাতে পৌঁছানোর পর তা’ আর আখড়ায় ফিরে আসেনি।”
লালনগীতির সংগ্রাহক মতিলাল দাশকে লালন শিষ্য ভোলাই শাহ বলেছিলেন-
“দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালোবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি নিয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনো উত্তর পাই নাই।”
কবিগুরুর জগতে লালন যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা বুঝতে এর বেশি জানার প্রয়োজন পড়ে না।লালনের গানের খাতাটি কবিগুরুর কাছেই রয়ে গিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন ও অসামান্য এক শিল্পীপুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে আপন মাধুরী দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের মরমী মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর হলে হয়তো লালন ফকিরের মতো মরমী কবি হতেন, আর লালন শিক্ষিত হলে হয়তো হতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবি। রবীন্দ্রমানসে লালনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে কালজয়ী এই দুই গীতি প্রতিভা সম্পর্কে এমনটা বলাই যায়।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাউল লালন ফকির।
একজন মানুষের জীবন ও কর্ম-পরিধির আলোকে বাঙালী সংস্কৃতির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁর ভেতর সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ ঘটেছে বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ ও মননশীলতার উপাদানসমূহ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রবির ন্যায় উজ্জ্বলতম। তাঁকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মাঝে পরিচয় করে দেয়ার প্রচেষ্টা মূর্খতা বা ধৃষ্টতা। তবুও তাঁর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সবকিছু ছাপিয়ে একটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিশেষণকেই আমরা বেশী ব্যবহার করি – ‘কবিগুরু’।
কবিগুরুর জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৯৪১-এ। এই প্রায় আশি বছরের জীবনের সময়কালে বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সমাজ, বাংলা সাহিত্য তাঁর অবদানে এতো ব্যাপকতম বিস্তৃত; তা’ পরিমাপের কোনো মাপকাঠি অদ্যাবধি কোন বাঙ্গালী লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক, বা বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধজনেরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হননি। বাংলা সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নেই – কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান ইত্যাদি যেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সফল পদচারণা পরিলক্ষিত হয় না। গুণগত ও পরিমাণগত উভয়দিকে তিনি অপ্রতিদ্বন্ধী ও অনতিক্রম্য।
বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন হতে আজ পর্যন্ত কেহই তাঁর কর্ম পরিধিকে স্পর্শ করতে পারেনি। রবীন্দ্রোত্তর কবি সাহিত্যিকবৃন্দ কমবেশি সকলেই রবীন্দ্রনাথের আলোকচ্ছটায় প্রভাবিত। বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদা এনে দিয়েছেন।
বৈশ্বিক সমাজে বাংলা ভাষাকে স্বকীয় প্রভায় উচ্চাসনে আসীন করেছেন তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’র নোভেল প্রাপ্তির মাধ্যমে। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় রচনা – সেই চর্যাপদ হতে রবীন্দ্র-পূর্ব সাহিত্য, বাংলা ভাষায় চিন্তা-চেতনার প্রকাশ যতই বলিষ্ঠ ও সম্মৃদ্ধশালী হোক না কেনো, বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে বাংলা ভাষা ও বাঙালীদের স্বকীয় মর্যাদায় পরিচিতি পায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্মে, চিন্তা-চেতনায়, নিজস্বতায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অনন্য।
গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনন্য রচনা। যার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে এনে দিয়েছে ১৯১৩ সালে নোভেল পুরস্কার প্রাপ্তির সম্মান ও মর্যাদা। বাংলা সাহিত্যকে এনে দিয়েছে বিশ্ব সমাজে পৃথকভাবে পরিচিতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে একটি সম্মৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ তা’ প্রতিভাত করে তুলেছে বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতি পরিমন্ডলে।এই গীতাঞ্জলি কাব্যের অন্তর্গত অধিকাংশ রচনাই গান। এই সকল গান বা গীতগুলোর সাথে অনেকটা সাযুস্য খুঁজে পাই বাংলার বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এর রচনার সাথে। খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলে মনে হয় গ্রাম্য শব্দ বিন্যাসের ভাবধারা ও চেতনাগুলো পরিশীলিত ভাষায় পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে গীতাঞ্জলিতে।
লালন গীতির কোন লিখিত রূপ লালন সাঁইয়ের স্বহস্তে না থাকার কারণে তাঁর ভাব শিষ্যদের কন্ঠে বা খাতায় মূল ভাবাদর্শের রূপখানি অনেকাংশে বিকৃত হয়ে গিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এমনকি তাঁর দেহান্তরের পরে বহু সংগ্রাহক ও সংকলকগণও সংশোধনের নামে যথেচ্ছ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তথাপি লালন প্রেমিক বা লালন ভাবাদর্শে বিশ্বাসীগণ লালনের বাণীকে অর্থাৎ, লালন সঙ্গীতকে – তাঁর দর্শনকে বা লালনের স্বকীয় প্রভাময় ভাবাদর্শকে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছেন। বহু ত্যাগ-তিতীক্ষা আর শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। তাঁরা সংখ্যায় অনেক। সেই ফকির লালন শাহের জীবনকাল থেকে শুরু করে আজ অবধি সেই সকল জ্ঞানী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কর্ম প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। ঐ সকল জ্ঞানী অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহক ও সঙকলকদের মধ্যে আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে একজনকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। তিনি হলেন মহৎ প্রাণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি মহারাজ ফকির লালন শাহের প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসা আর গুরু ভাবজ্ঞানে লালন সঙ্গীতের সংগ্রাহক ও সঙকলনকারী হিসেবে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন।
লালন সাঁই সব সময় বিলীন থাকতেন পরমাত্মার মাঝে। আর সেই অসীম পরম আত্মার মাঝেই খুঁজে বেড়িয়েছেন মানবসত্ত্বার মানুষকে। মানবতাই তাঁর নিকট ছিল বিশেষ গুরুত্ববহ। তাই তিনি সহজেই বলতে পারতেন প্রচলিত ধর্ম মানুষের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করে। পরমাত্মার সাথে মানুষের একাত্ম হওয়ার ধর্মই মানবতার ধর্ম। যা মানবাত্মার দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁর ভাষায় –
‘ডানে বেদ, বামে কোরান,
মাঝখানে ফকিরের বাণী,
যার হবে সেই দিব্যজ্ঞান
সেই-ই দেখতে পায়
আর এই বাণীর দ্যোতনা খুঁজে পাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়।
তিনি সীমাবদ্ধতার ভেতর খুঁজেছেন অসীমের আলোক রশ্মি। অন্য এক ধরণের ভাব দর্শনে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন অসীমত্বের মাঝে অস্তিত্বের সন্ধান। বিশালত্বের মাঝে খুঁজে ফিরেছেন স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব। পরমের মাঝে বিলীন হওয়ার আনন্দরাশি। তাই তিনি লেখনীর তুলিতে ছাপিয়ে তোলেন সেই আকাঙ্খার সুর ও ছন্দ –
“সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।”
অনন্ত কালচক্রের নানা পর্বে লোকান্তরের মহাপুুরুষগণ ধীরস্থিরতা, ভারসাম্য ও শান্তি পূণঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ জগতে জন্ম গ্রহন করেন। সেই সকল মহা মানবগণ তাঁর চেয়ে অধিকতর শক্তিধর, গুণধর বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ত্বের কাছে নিজেকে সমর্পন করে থাকেন। আর এই আত্মসমর্পন নীচতা নয়; হীনতা নয়। এ হলো শক্তির উন্মেষ। সেই শক্তি হলো ভক্তির শক্তি। শক্তিহীন অবস্থায় যেমন শক্তিমানকে ষ্পর্শ করা যায় না; ক্ষুদ্রতা দিয়ে যেমন বৃহৎকে বুঝা যায় না; পরম সত্যকে তেমনি খন্ডিত বিচারবুদ্ধি বা সংকীর্ণতা দিয়ে অনুধাবন করা যায় না। এমনটিই ঘটেছে ফকিররাজ লালন শাহের মূল্যায়ন প্রচেষ্টায়। তাই হয়তো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং লালন দর্শনের শক্তির মূল্যায়নে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাসাধ্য পরিমার্জনা করে ফকির লালন শাহের কুড়িটি গান সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৯০৫ সালে (১৩১২ সালের আশ্বিন সংখ্যায়) ‘‘হারামনি’’ বিভাগে প্রকাশ করেছিল। অর্থাৎ কবিগুরুর চিন্তা-চেতনায় বাউল লালন শাহের সঙ্গীত সম্পদ ছিল অমূল্য সম্পদ। তাই ‘‘হারামনি’’ শিরোনামে স্থান পেয়েছিলো লালনগীতি।লালন সঙ্গীতের দার্শনিক ও নান্দনিক প্রভাব যেমন কবিগুরুকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে তুলেছিলো – তেমনি শহুরে শিক্ষিত সমাজকে নাড়া দিয়ে গেলো।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় -‘আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ- আলোচনা হতো। আমার অনেক গানে আমি বহু সুর গ্রহন করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সাথে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গিয়েছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স- শিলাইদহ (কুস্টিয়া) অঞ্চলের এক বাউল একতারা হাতে বাজিয়ে গেয়েছিল –
‘কোথায় পাবো তাঁরে – আমার মনের মানুষ যেঁরে।
হারায়ে সেই মানুষে- তাঁর উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে’
(এই গানটি গেয়েছিল-ফকির লালন শাহের ভাবশিষ্য গগন হরকরা। যার আসল নাম বাউল গগন চন্দ্র দাম।)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের ভাষায়, ঐ বাউলের গানের কথা ও সুরের মাধুর্য আমাকে এতোই বিমোহিত করেছিলো যে, আমি সেই সুর ও ছন্দে বাংলাদেশকে মাতৃরূপ জ্ঞানে লিখেছি –
‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাঁজায় বাঁশি’
যা বর্তমানে রক্তস্নাত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জাতীয় সঙ্গীত।
রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে মাতৃ-জ্ঞানে ভালোবেসে, শ্রদ্ধায়, ভক্তি-প্রেমে, অন্তরে সমস্ত চেতনায় লালন শাহের সুর ও ছন্দে রচনা করেছিলেন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’। অর্থাৎ, আমাদের রক্তের ঝর্ণাধারার বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় সঙ্গীত ভাষা ও শব্দ বিন্যাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যমান হলেও; সুর ও ছন্দে এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে বাউল সম্রাট লালন শাহের অবদানকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গীতধারায় যদি আমরা আধ্যাত্মিকতার চেতনায় নিবিষ্টতায় রসাস্বাদন করি তা‘হলে আমরা দেখবো যে লালনের দর্শনের বা লালনের বাণীর পরিশীলিত রচনার ধারাবাহিকতা।লালনের বাণীতে বিনয় ও মানবীয় আমিত্ব শূন্যতার এক কৌশল মাত্র। গুরুর চরণে নিজেকে অধম ও গুরুত্বহীনভাবে তুলে ধরে গুরুকে সর্বোত্তমরূপে প্রকাশ করার এক কৌশল সাঁইজী তুলে ধরেছেন তাঁর সুরে ও কথায়। পরম আত্মাকে কল্পনা করেছেন গুরুর ভনিতায়। সেই কথাই যেন আমরা শুনতে পাই কবিগুরু রবী ঠাকুরের কন্ঠে –
‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।
সুরের আলো ভূবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষান টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধ্বনী।’
রবীন্দ্রনাথ অরূপের (নিরাকার) অপরূপ রূপে অবগাহনের নিমিত্তে অতল রূপ সাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন (অমূল্য রতন) আশা করি, তাঁর ভাষায়-
‘রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।’
লালন তাঁর একতারার তারে সুরে ও ছন্দে গেয়ে গেছেন –
‘রূপের তুলনা রূপে।
ফণি মণি সৌদামিনী
কী আর তাঁর কাছে শোভে
যে দেখেছে সেই অটল রূপ
বাক্ নাহি তার, মেরেছে চুপ।
পার হলো সে এ ভবকূপ
রূপের মালা হৃদয়ে জপে।’
এই রূপের তুলনা মানবসত্ত্বায় নিহিত বস্তুমোহমুক্ত নিষ্কামী মহা মানবের স্বরূপ। যে মহা মানব সম্যক গুরুদেবের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পিত চিত্তে কঠিন ধ্যানব্রত অবস্থায় শিক্ষা গ্রহন করেন। যেখানে অরূপে (অস্থিত্বহীনতায়) খুঁজে ফেরে রূপের সন্ধান। যেখানে ‘নিজেকে জানা’ এর জন্য পরিপূর্ণ আত্মদর্শনে ব্যাপৃত থাকে।
তাই লালন ফকির দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছেন –
‘যার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পারলেরে
যাবে অচেনারে চেনা
আত্মরূপে কর্তা হরি,
নিষ্ঠা হলে মিলবে তাঁরই ঠিকানা।
ঘুরে বেড়াও দিল্লি লাহোর
কোলের ঘোর তো যায় না’
ধর্ম তত্ত্বে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য বৈরাগ্য সাধন প্রক্রিয়ায় বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, অথবা মক্কা-কাশীতে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেননি লালন শাহ; তেমনি তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লালন দর্শনের মতোই ঈশ্বরের মহিমা খুঁজে ফিরেছেন মানুষের মাঝে। মানুষই ঈশ্বর, মানুষই দেবতা, মানুষের মাঝেই পরমাত্মার অস্থিত্ব লীন।
তাই লালন শাহের কন্ঠে যেমন শুনি-
‘ভবে মানুষ গুরুনিষ্ঠা যার।
সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার
নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে
আকার সাকার হইল সে
যে জন দিব্যজ্ঞানী হয়,
সেই জানতে পায়
কলি যুগে হল মানুষ অবতার’
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন শাহের ভাব দর্শনের দ্যোতনাকে আরও উচ্চমার্গে তুলে ধরেছেন।মনে হয় লালনের চিন্তা-চেতনাকে শালীন ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন স্বয়ং কবিগুরু। মার্জিত ভাষার পরিশীলিত সুরের মাধুর্য দিয়ে কবিগুরু একতারার সুরের স্থানে বীণার তারে ঝংকৃত করেছেন মানব ও মানবতার মাঝেই পরমাত্মার অস্তিত্ব। সেই পরমাত্মাকে পেতে হলে আমিত্বের অহংবোধকে লীন করে দিতে হবে মানুষ-গুরু সাধনে; মানবতার পরাকাষ্ঠা দেদীপ্যমান করে।
কবিগুরুর ভাষায় তা হলো –
‘ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পরে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ –
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে –
তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার ‘পরে।’
অপরদিকে, ফকির লালন শাহ মানবদেহে নিহিত আলোকিত সত্তার উন্মেষের ইচ্ছায় স্বীয় কন্ঠে উচ্চারণ করেন –
‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই
মূল হারাবি’
মানুষ ছাড়া মনরে আমার
দেখিরে সব শূণ্যাকার
লালন বলে মানুষ আকার
ভজলে পাবি’
লালন ফকির তাঁর পরমাত্মার সাথে মিলনের প্রচন্ড আকাঙ্খা তাঁকে উন্মাতাল করে রাখতো, তাই সে প্রভুর সাথে মিলনের আকাঙ্খায় বেদন সুরে গেয়ে বেড়ায়-
‘মিলন হবে কতোদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে।
ঐ রূপ যখন স্মরণ হয়
থাকে না লোক লজ্জার ভয়
লালন ফকির ভেবে বলে সদাই
ও প্রেম যে করে সেই জানে’
প্রভুর সাথে মিলনের ইচ্ছা লালনকে যেমন চাতক প্রায় জ্যোৎস্নালোকের প্রত্যাশায় দিন গুনতো, তেমনি প্রভুর সান্নিধ্য পাবার আশায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে গাইতেন –
‘যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন,
সে কথা রয় মনে ।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।’
অথবা
‘আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।’
লালন শাহের প্রয়াণের সময়কালে কবিগুরুর পূর্ণ যৌবনকাল। তখন তাঁর বয়স ২৮/২৯ বছর। যে ‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং বাংলা ভাষাকে এনে দিয়েছে সুনাম, সম্মৃদ্ধি ও বিশ্বজনীনতা। সেই গীতাঞ্জলির প্রতিটি ‘গীত’ ধীর-স্থীরতার সাথে পাঠ করলে নিজের অজান্তে মনে হবে – এ কথাগুলোতো তাঁর পূর্ব-পুরুষ বা গুরু বাউল কবি ফকির লালন শাহ আগেই বলে গেছেন। অর্থাৎ, গীতাঞ্জলির গানগুলো লেখার সময় কবিগুরু প্রচন্ডভাবে বাউল কবি লালনের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।
কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এশিয়ার প্রথম নোভেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেভাবে দুই বাংলায় বাঙালীগণ উচ্ছসিত ও উদ্বেলিত হয়ে স্মরণ করেন; সেইরূপ হয়না বাউল সম্রাট লালন শাহের ক্ষেত্রে। অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল উৎস এবং প্রেরণা সবই লালন সাঁইয়ের কারণে।